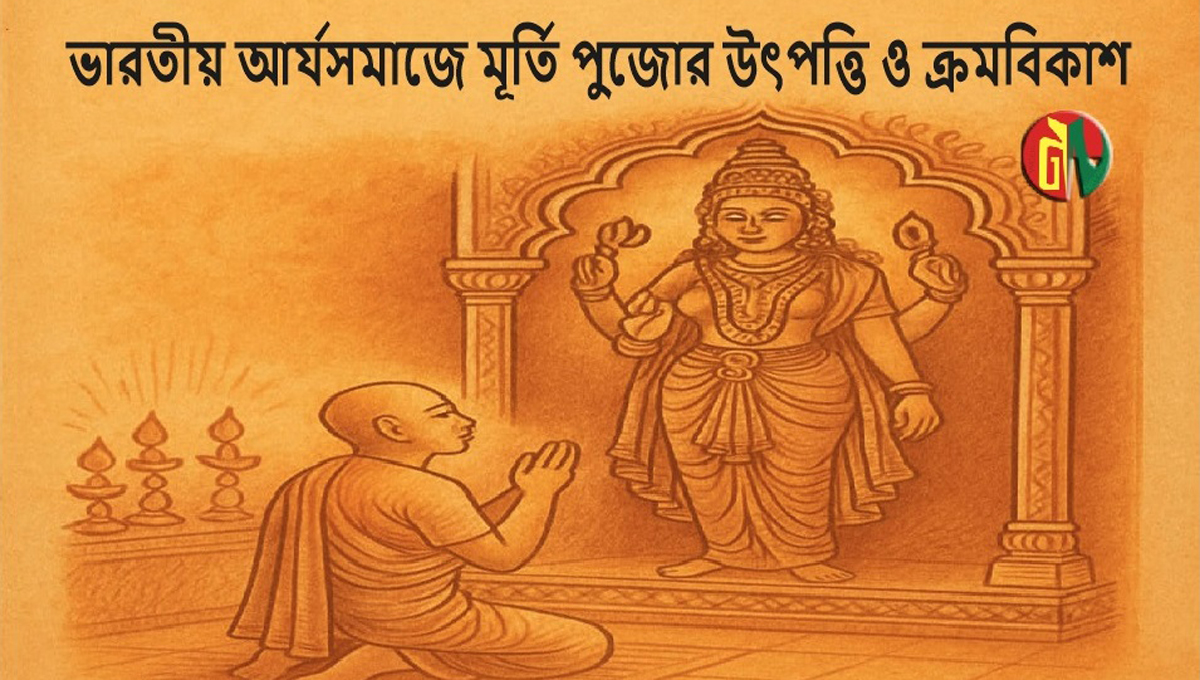উত্তম মণ্ডলঃ
বৈদিক আর্যদের ধর্মজীবন ছিল মূলত: উপলব্ধিময় এবং তা ছিল যজ্ঞভিত্তিক। বেদে মূর্তিপুজোর কোনো উদাহরণ নেই। তাই বলা যায়, মূর্তিপুজোর সঙ্গে বৈদিক আর্য ধর্মজীবনের কোনো সংস্রব ছিল না। এখন প্রশ্ন, তাহলে আর্যরা মূর্তিপুজোর ধারণাটা পেয়েছিল কোথা থেকে? উত্তরে বলা যায়, অবশ্যই অনার্যদের কাছ থেকে। অনার্যরা গাছ-পাথরের পুজো করতো। আর্যরা অনার্যদের এই পুজো পদ্ধতিকে নিজেদের যজ্ঞভিত্তিক উপাসনার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিল। এভাবেই আর্য-অনার্যের মিলনে গড়ে উঠলো যজ্ঞময় পুজো পদ্ধতি।
পরবর্তীকালে এই পুজোকে কেন্দ্র করেই উদ্ভব ঘটলো শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য ও বৈষ্ণব---এই পাঁচটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের। বলা যায়, বৈদিক যজ্ঞভিত্তিক উপাসনা পদ্ধতির ধ্বংসস্তূপ থেকেই এই পাঁচটি সম্প্রদায়ের জন্ম হলো।এরপর শুরু হলো, রূপমূলক উপাসনা’–“রূপং দেহি, জয়ং দেহি…।” আর্যদের যজ্ঞভিত্তিক উপাসনা আর অনার্যদের গাছ-পাথর প্রভৃতি পুজোর সংমিশ্রণে তৈরি হলো এক নতুন ধর্মীয় জীবনধারা, যা মূলত আজকের হিন্দুধর্ম বলে পরিচিত।
মূর্তিপুজো একদিকে যেমন সমাজের বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত মানুষদের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করেছে, অন্যদিকে তেমনি সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে তৈরি করেছে দূরত্ব। মূর্তিপুজোয় প্রতিমা শিল্পী কাজ পেয়েছে, পুরোহিত কাজ পেয়েছে, ফুল-মালী কাজ পেয়েছে, ঢাকি কাজ পেয়েছে, শোলা শিল্পী কাজ পেয়েছে এবং এভাবে সমাজের সব অঙ্গগুলি মূর্তিপুজোয় একীভূত হয়েছে। অন্যদিকে, বৈদিক আর্য ঋষিদের ধর্মীয় জীবন অনুশীলনের উদার স্রোত হারিয়ে গেছে সম্প্রদায়বাদীদের সংকীর্ণ মনোভাবের কাছে। যেমন, শৈবরা শিবকে, শাক্তরা শক্তিকে, সৌররা সূর্যকে, গাণপত্যরা গণপতিকে এবং বৈষ্ণবরা বিষ্ণুকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করতে গিয়ে একে অপরের নিন্দায় মুখর হয়েছে। বৈষ্ণবরা তো দেবাদিদেব শিবকে বানিয়েছেন কৃষ্ণের “কিঙ্কর।” এটি একটি উদাহরণ মাত্র। আসলে কোন্ দেবতার রূপ বড়ো, তা নিয়ে হিন্দুধর্মের এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে অপর সম্প্রদায়ের চললো লাগাতার বিবাদ, যার অনিবার্য পরিণতি হলো আর্যধর্মের অভ্যন্তরে ঐক্যবদ্ধজীবনে ভাঙন। এই ভাঙন একে অপরের বিশ্বাসে আঘাত হানলো এবং এর ফলে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয়—সব দিক দিয়েই অনৈক্য দেখা দিলো।
তাই বলা যায়, মূর্তিপুজো সামাজিক জীবনে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করলেও উল্টোদিকে এই মূর্তিপুজোর ফলে বৈদিক আর্যদের বিশ্বকে প্লাবিত করার শক্তি হারিয়ে গেল। পরবর্তীকালে হিন্দুধর্মের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থসিদ্ধির জন্য জ্ঞান ও ভক্তির বিভিন্ন আধুনিক ব্যাখ্যা (অপব্যাখ্যা? ) খ্রিস্টানদের মধ্যযুগীয় মুক্তিপত্র বিক্রির মতোই অবাস্তব এবং স্বার্থসিদ্ধির পথ বলে গণ্য হয়ে গেল। বহু শাস্ত্রকেই এক শ্রেণির মানুষ তালি-তাপ্পি মেরে “প্রক্ষিপ্ত” করেছে, যার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য নেই। এরপর শাস্ত্র বদলের ফলে মূর্তিপুজোর মধ্যে জীবত্ব পরিহারের বদলে জীবত্ব প্রতিষ্ঠাই লক্ষ্য হয়ে উঠলো। সব ধর্মীয় তত্ত্ব শেষ পর্যন্ত তৈরি হয়ে গেল অর্থ রোজগারের জন্যই। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ চাল-কলা বাঁধা বিদ্যে শিখতে চান নি। অথচ এর বিপরীতে এক শ্রেণির মানুষ মূর্তিপুজোর সঙ্গে বংশপরম্পরায় যুক্ত থেকে আর্যদের উপলব্ধিজাত জ্ঞানকে ভক্তিবিরোধী বলে প্রচার করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে চলেছে আজও। অথচ যে ভক্তি যে তত্ত্বস্বরূপের ভজনা করে, জ্ঞান তারই ভজনা করে। কারণ, তত্ত্বস্বরূপের অবধারণার আরেক নাম হচ্ছে ভজন। এক স্বরূপের দুটি ভিন্ন নাম মাত্র। যেমন, একজনের দুটো নাম শ্রীকৃষ্ণ ও পার্থসারথী, তেমনি জ্ঞান ও ভক্তি এক উপাসনার দুটো নাম। কিন্তু এক শ্রেণির মানুষ ধর্মপ্রচারের ঠিকে নিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে জ্ঞান ও ভক্তিকে আলাদা করে দিয়ে হিন্দু সমাজে বিভেদের মাত্রা বাড়িয়ে চললো।
ঋগ্বেদে বলা হয়েছে, ---
"সুপর্ণং বিপ্র কবয়োবানোভিরেণং বহুধা কল্পয়ন্তি।" অর্থাৎ পক্ষী একই আছেন, কিন্তু তাঁর বহুধা রূপ শুধুমাত্র পণ্ডিতের বুদ্ধিকৃত। এখানে "পক্ষী" হচ্ছেন ব্রহ্ম সমান। ব্রহ্ম মৌলিক, কিন্তু তাঁর দুই বা বহুধা রূপ হচ্ছে বুদ্ধি দিয়ে তৈরি। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, এক ব্রহ্ম আবার "বহু" হলেন কেন? এর উত্তর হলো, মানুষের উপাসনাকে সরল করার জন্য। রূপহীনকে মানুষ ধ্যান করবে কি করে? সেজন্য সাধকের সামনে রাখা হলো লক্ষ্মণযুক্ত বা রূপযুক্ত প্রতীক। আর এই প্রতীকী উপাসনার নামই হলো "মূর্তিপুজো।"
হিন্দু দেবদবীর মূর্তিগুলি সব ব্রহ্মের প্রতীক হিসেবে গণ্য এবং সেজন্য এইসব দেবদেবীরাও হলেন ব্রহ্মাত্মক। দেবদেবীরা এখানে উপলক্ষ্য মাত্র, সাধকের আসল লক্ষ্য হলো ব্রহ্ম। তাই মূর্তিপুজো দিয়ে সাধকের অক্ষমতা দূর করতে তাঁর সাধনায় সাহায্য আরোপ করা হয়েছে। এই সাহায্য আরোপের অন্য নাম মূর্তিপুজো। কিন্তু মূর্তিপুজো দিয়ে যে সাহায্য আরোপের মাধ্যমে সাধকের অক্ষমতা দূর করার চেষ্টা হয়েছিল, পরবর্তীকালে সেই মূর্তিপুজোকে ঘিরে তৈরি হলো বেশকিছু ভ্রান্ত কুসংস্কার।
যেমন, অব্রাহ্মণদের পুজোপাঠ করা যাবে না, চণ্ডীপাঠ করা যাবে না, ইত্যাদি। উদাহরণ অনেক লম্বা হয়ে যাবে। এর ফলে মূর্তিপুজোর যে লক্ষ্য ছিল ব্রহ্ম, তা থেকে মানুষ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেল। আর এর পরিণামে বহু টুকরো টুকরো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হলো মূল আর্যধর্ম থেকে। অন্যদিকে, সমস্ত দেবদেবীরা ব্রহ্মলক্ষ্যচ্যুৎ হয়ে নিজের নিজের সম্প্রদায়ের কাছে বড়ো হয়ে উঠলেন। পুরাণের পাতা ওল্টালেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। যেমন শাক্ত পুরাণে দেখা যায়, বিষ্ণু-কৃষ্ণ-শিব-ব্রহ্মা---সকলেই শাক্তের উপাস্য দেবী শক্তির উপাসক হয়ে গেছেন। আবার বৈষ্ণব পুরাণে শিব-কালী-ব্রহ্মা---সবাই বৈষ্ণবের উপাস্য দেবতা বিষ্ণুর কাছে নগণ্য হয়ে গেছেন। সর্বত্র এই ধরণের একপেশে বিবরণ লেখা হয়েছে পুরাণের পাতায়।
এর ফলে এক সম্প্রদায়ের দেবতার মূর্তি অন্য সম্প্রদায়ের কাছে "পুতুল" হয়ে গেছেন। পুতুল নিয়ে এই মত্ততার নামই হলো "পৌত্তলিকতা।" এই পৌত্তলিকতা হলো মূর্তিপুজোর মারাত্মক বিষফল। এভাবে মূর্তিপুজোর নামে ধর্ম নিয়ে হিংসা-হানাহানির যে শুরু, তা আজও চলছে। তাই এখনো এক শ্রেণির ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভক্ত বলেন, কৃষ্ণ "কালী" হয়েছিলেন, কিন্তু কালী কখনও "কৃষ্ণ" হোন নি। এভাবে বৈদিক আর্যধর্ম সংকুচিত হয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে মূল হিন্দু সমাজের দেহটাই খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে। বৈদিক ঋষিদের উদার আর্যধর্মের ঐক্য বিনষ্ট হয়ে তৈরি হয়েছে আজকের খণ্ডিত হিন্দু সমাজ। এখনও বহুধা বিভক্ত হিন্দু সমাজ অনেকটা এই কারণেই।তথ্যসূত্র:
১) রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি (৩ খণ্ড): মানিকলাল সিংহ, বাঁকুড়া, ১৯৮২, ১৯৮৩
২) রাঢ় বাংলার ইতিহাস ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য: মমতা বৈষ্ণব, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬
৩) বাংলার লোকসংস্কৃতি: আশুতোষ ভট্টাচার্য, এন.বি.টি, দিল্লি, ১৯৮৬
৪) বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ও বাঙালি বৌদ্ধদের ক্রমবিবর্তন: সাধনকমল চৌধুরী, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা
৫) হিন্দুধর্মে জাতিবর্ণভেদ ও বৌদ্ধধর্ম: অনিল কুমার সেনগুপ্ত, বাউলমন, কলকাতা, ২০০৪
৬) প্রাচীন ভারত: সমাজ ও সাহিত্য: সুকুমারী ভট্টাচার্য, কলকাতা, ১৩৯৬
৭) ধর্ম ও জীবন: রণজিৎ কুমার সেন, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, ১৯৮৮
৮) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (বৈশ্যকাণ্ড, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৩২০: নগেন্দ্রনাথ বসু
৯) Studies in the Puranic Records on Hindu Rites and Customs: R.C. Hazra, Dhaka, Bangladesh, 1940.
১০) The Vedic Age: R.C. Majumder (Ed), 1951.
১১) Vedic Mythology: A.A.Macdonell, Strassburg, 1897.
১২) Indigenous Indians: Agastya to Ambedkar: Elst. Koenraad, New Delhi, 1993.